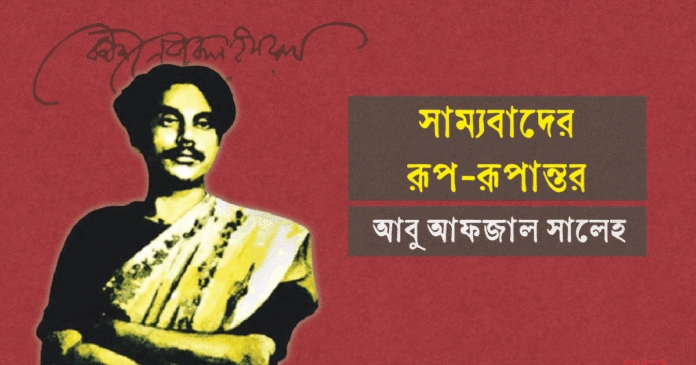কবিতা একটি জনপ্রিয় শিল্পমাধ্যম। শক্তিশালী প্রতিবাদ, সহানুভূতি আদায় থেকে শুরু করে নাগরিক অধিকার এমনকি শিল্পসাহিত্যের অন্যান্য মাধ্যমে কবিতার ব্যবহার অভিযাত্রাকে করে তুলে মহান ও শক্তিমান। অশুভ ও অমানবিক শক্তির বিরুদ্ধে ছোট্ট এ মাধ্যমটি বড় অস্ত্র হতে পারে। দেশবিদেশের বিভিন্ন আন্দোলন ও অভিযাত্রায় তা প্রমাণিতও। কাজী নজরুল ইসলাম উল্লিখিত সবকিছুতে ব্যবহার ও প্রয়োগে বাঙালির অগ্রনায়ক। নির্যাতিত ভুক্তভোগীদের জন্য তাঁর হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হয়েছে। তাইতো ‘আমার কৈফিয়ৎ’ কবিতার শেষে বলেছেন, ‘প্রার্থনা করো যারা কেড়ে খায় তেত্রিশ কোটি মুখের ঘ্রাস,/যেন লেখা হয় আমার রক্ত-নেশায় তাদের সর্বনাশ’। এ কথাতেই বুঝে নেওয়া কঠিন নয় যে, সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নজরুল কতটা আন্তরিক ও কতটা অগ্রগামী।
সমাজ ও রাষ্ট্রের নানা অসংগতি কবিকে ব্যথিত করেছে। এই অসুন্দরগুলো মুছে দিতে চান তিনি—গড়তে চান সাম্যের বিশ্ব, বৈষম্যহীন পৃথিবী। দীর্ঘদিন চলে আসা রাষ্ট্র ও সমাজের বিভিন্ন স্তরের অনিয়ম, বৈষম্য, অবজ্ঞা, অবহেলা, শোষণ, নিপীড়ন ইত্যাদির বিরুদ্ধে কবিতায় ও অন্যান্য সাহিত্যশাখায় উচ্চকিত ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। তাঁর মূলনীতি—’গাহি সাম্যের গান’। তাঁর চিন্তার ভরকেন্দ্র হচ্ছে মানবতাবোধ—সমতা বিধান—’গাহি সাম্যের গান/মানুষের চেয়ে বড় কিছু না, নহে কিছু মহীয়ান,/নাই দেশ-কাল-পাত্রের ভেদ, অভেদ ধর্মজাতি,/সব দেশে, সব কালে, ঘরে-ঘরে তিনি মানুষের জ্ঞাতি’ (মানুষ)। ‘আইন তার নিজস্ব গতিতে চলবে’ নিশ্চিত করাই কবির মুখ্যবিষয়। রাষ্ট্র ও সমাজের সব স্তরে সমতা নিশ্চিত করতেই হবে তাঁর আকাঙ্ক্ষা ও মূল দাবি। তাঁর বিদ্রোহী কবিতা উৎকৃষ্টতম উদাহরণ—সম্ভবত বাংলা ভাষারই। ‘আমার কৈফিয়ৎ’ নজরুলের আত্মদর্শনের উপলব্ধি। সমাজের বিদ্যমান অশুভ দিকগুলোর বিরুদ্ধে তাঁর অবস্থান। বিভেদমূলক পার্থক্যগুলো ভুলে ঊর্ধ্বে উঠার পরামর্শ তাঁর। এজন্য কবিতায় তাঁর কণ্ঠস্বর হয়েছে জ্বালাময়ী, চরম। ভাষা, শব্দচয়ন, অলংকার প্রভৃতি ব্যবহার ও দক্ষ প্রয়োগে পার্থক্যগুলো দেখিয়েছেন। আমেরিকান কবি হুইটম্যানের আমেরিকানবাদ, ও মাই ক্যাপ্টেন, ব্যক্তিগণতন্ত্রবাদ ইত্যাদি যেন নজরুলের কাণ্ডারি, বিদ্রোহী প্রভৃতি। নজরুলের আমি’তে আমিত্ব নেই, আছে শোষণমুক্ত, বৈষম্যমুক্ত সমাজ গড়ার অঙ্গীকার, আকাঙ্ক্ষা। নজরুলের কবিতায় সাম্যবাদ বিষয়টি ব্যাপক বিস্তৃতি রয়েছে। সমস্ত মানবতার সমতার দিকে।
অমানবিক শক্তির বিরুদ্ধে নজরুলের সরাসরি অভিযান। শান্তিস্থাপন ও বৈষম্যমুক্ত সমাজ গড়তে এসব দেওয়াল ভেঙে ফেলতে হবে। নজরুল উপড়ে ফেলতে চান—’আমি উপাড়ি ফেলিব অধীন বিশ্ব অবহেলে নব সৃষ্টির মহানন্দে’ (বিদ্রোহী)। ফরাসি বিপ্লব (১৭৮৯–১৭৯৩) এর স্লোগান গান ‘সাম্য, সমতা এবং ভ্রাতৃত্ব’ রোমান্টিক কবি শেলীর মানসে বিরাট প্রভাব ফেলেছিল। কাজী নজরুল ইসলাম রাষ্ট্র, সমাজ ও বিভিন্ন স্তরের শাসক-নেতৃত্বের অনিয়মের বিরুদ্ধে কলম ধরেছেন, সরাসরি যুদ্ধও করেছেন। শোষিত শ্রেণিদের জন্য বিরাট অনুপ্রেরণার নাম কাজী নজরুল ইসলাম। সাম্যবাদ নীতি বাস্তবায়নের জন্যই তিনি ছিলেন অন্তঃপ্রাণ। সাম্যবাদ রুখে দিতে নজরুল যুগে যুগে আসেন। নজরুলের কালবৈশাখি, টর্পেডো, সাইক্লোন, অর্ফিয়াসের বাঁশিও কিন্তু কম জোরালো নয়। মানুষ ছিল তাঁর মূল উপজীব্য। নজরুলের ‘আমি’-এর মধ্যে আমিত্ব নেই। নজরুলের ‘আমি’ মুক্তিপিয়াসিদের পথপ্রদর্শক; অন্যায়ের প্রতি, অবিচারের প্রতি প্রবল বিরোধিতা। নজরুলের ‘আমি’ সমস্ত অত্যাচারী শাসকের প্রতি অস্ত্র, কুসংস্কারের প্রতি ঘৃণা। নজরুলের আমি নষ্ট করেছে ক্ষমতাবানদের তথাকথিত আমিত্ব।
কুলি ও মজুর প্রতীকী হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এরা ঘাম ও রক্ত দেওয়া সমাজের প্রতিনিধি। যাদের মূল অবদানে এ সভ্যতা গড়ে উঠেছে। সমতা নিশ্চিত করে তাদের অধিকার আদায় করার অঙ্গীকারের নাম কবি নজরুল। ‘সভ্যতার সংঘাত’ এড়িয়ে যেতে হবে। কেন সংঘাত হবে? উন্নয়ন ও সভ্যতা নির্মাণে সবাই তো সমান অংশীদার। তবে, উঁচু-নিচু শ্রেণি থাকবে কেন? যাদের মুখ্য অবদান তারা কেন অবহেলিত থাকবে? এসব প্রশ্নের জবাব পাওয়া যায় ‘কুলি-মজুর’ কবিতায় । ‘হে দারিদ্র্য, তুমি মোরে করেছ মহান/তুমি মোরে দানিয়াছ খ্রিস্টের সম্মান’ বলে দারিদ্র্যকে স্বীকৃতি দিয়েছেন কবি নজরুল ইসলাম। বাস্তবতা থেকেই গড়ে উঠতে হবে। মানবতাবাদী কবির প্রধান লক্ষ্যই হচ্ছে সমাজের বিরাজমান নানান অসংগতি, অবিচার, অন্যায়, অনাচার ও বৈষম্যের প্রতি প্রতিবাদ করা, মূলে আঘাত করা। কবি নজরুল এক্ষেত্রে শতভাগ সফল। সমাজে ঘাপটি-মেরে-থাকা অমানুষদের প্রতি ক্ষোভ ও বিদ্রোহ উগরে দিয়েছেন তিনি, ব্রিটিশ সরকারের অন্যায় কাজ বা পদক্ষেপের প্রতি রুখে দাঁড়িয়েছেন। এজন্য একাধিকবার জেল-জুলুমের শিকার হয়েছেন তিনি। তাঁর ৫টি গ্রন্থ বাজেয়াপ্ত হয়েছে। আগ্নেয়গিরির মতো জ্বলন্ত হয়ে প্রতিবাদী হয়ে উঠলেন শাসকের প্রতি, সমাজের ভ্রান্তনীতির প্রতি। তিনি মানবতার পক্ষে আসলেন ‘ধূমকেতু’ হয়ে।
‘আমার কৈফিয়ৎ’ কবি নজরুলের প্রতিনিধিত্বকারী একটি শ্রেষ্ঠতর কবিতা। কবিতাটি কবি নজরুলের আত্মোপলব্ধির জীবনদর্শন বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। নজরুলের ভাবনা বা চিন্তার প্রতিফলন ঘটেছে এ কবিতায়। কী কী করবেন, কী কী করা উচিত—তা তিনি এ কবিতায় তুলে ধরেছেন। কবিতার শুরুতেই নজরুল বলেন, ‘বর্তমানের কবি আমি ভাই, ভবিষ্যতের নই ‘নবী’!/কবি ও অকবি যাহা বল মোরে মুখ বুঝে তাই সই সবি’। তিনি আসলে মানবতার পক্ষেই ছিলেন। মানুষই তাঁর মূল লক্ষ্য। তিনি কোনো পক্ষে জড়িত হননি। নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে মানবতাই তুলে ধরতে চেয়েছেন। ফলে, বিভিন্ন দল, মত, ধর্মে বিভক্তরা তাকে প্রতিপক্ষের লোক বলে বিবেচনা করতো। কাজী নজরুল ইসলাম ধূমকেতুর মতো এসেছেন, হঠাৎ করেই। তিনি ‘ধ্বংস দেখে ভয় কেন তোর.. অসুন্দরের করতে ছেদন’ বলে অভয় দিয়েছেন। নতুন কিছু সৃষ্টি করতে হলে ধ্বংস অনিবার্য। পুরাতন ভেঙে নতুনের নতুনকে সম্ভাষণ করতে হবে। এজন্য কিছু ক্ষ্যাপা দামাল দরকার ‘ঐ ক্ষ্যাপেছে পাগলী মায়ের দামাল ছেলে কামাল ভাই (কামাল পাশা)’। বঞ্চিতদের পক্ষে আজীবন সংগ্রাম ও লড়াই। প্রেমের মধ্যেও তিনি বিদ্রোহী হয়েছেন। সাম্যবাদের জয়গান গেয়েছেন। এক্ষেত্রে আমরা কবি পিবি শেলীর কবিতার স্মরণ করতে পারি। তিনিও সকল প্রকার অন্যায়ের বিপক্ষে সাহসী উচ্চারণ করতেন। নজরুলের ‘বিদ্রোহী’ ও শেলীর ‘ওড টু দ্য ওয়েস্ট উইন্ড’ দুই কবির চেতনা ও দর্শনের সামগ্রিক মুখপত্র বলা যেতে পারে। অন্যায়, বৈষম্য, কুসংস্কার, বর্ণবাদ, ধর্মান্ধতা, দুর্নীতির বিরুদ্ধে কবিতায় জানিয়েছেন জ্বালাময়ী সুর।
সাম্যবাদের এমন জয়গান গাইতে গিয়ে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছেন কাজী নজরুল ইসলাম। সমাজ ও রাষ্ট্রের সব স্তরের অনিয়ম, স্বেচ্ছাচারিতা, বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন। মানুষ, সাম্যবাদী, ঈশ্বর, পাপ ইত্যাদি কবিতাসহ বিষের বাঁশি, সর্বহারা, সাম্যবাদ কাব্যগ্রন্থের অনেক কবিতায় সাম্যবাদের নীতি প্রকাশিত হয়েছে। সাম্যবাদী কাব্যগ্রন্থের বীরাঙ্গনা, নারী, রাজা-প্রজা, সাম্য, কুলি-মজুর, চক্রবাক কাব্যের ‘ওগো ও চক্রবাকী’ ইত্যাদি কবিতায় নারী প্রগতির কথা বলা হয়েছে। ‘সর্বহারা’ কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলোতে বিভিন্ন পেশার মানুষ ও তাদের অধিকার নিয়ে লেখা হয়েছে। ‘ধীবরের গান’, ‘শ্রমিকের গান’ ও ‘কৃষাণের গান’—এমন নামীয় কবিতাগুলো বিভিন্ন পেশার জয়গান করা হয়েছে। ব্রিটিশ শাসক ও মহাজন কর্তৃক শোষণ-বঞ্চনার কথা বলা হয়েছে। তাদের দাবি নিয়ে সোচ্চার হতে বলা হয়েছে। কবি নজরুল এসব দাবি বা অধিকার আদায়ে একাত্মতা প্রকাশ করে কবিতায় রূপ দিয়েছেন। এমন সব কবিতায় কবির সাম্যবাদী রূপ প্রবলভাবে ফুটে উঠেছে। ‘বিষের বাঁশি’ কাব্যগ্রন্থে কবি মুক্তিকামী মানুষের মনের কথা তুলে ধরেছেন। স্বাধীনতাকামী মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন। তৃণমূল মানুষের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেছেন। কলম ধরেছেন। তুলে ধরেছেন কবিতার পরতে পরতে। এসব কবিতার বাণী বর্তমানেও প্রাসঙ্গিক। ব্রিটিশরা পরাজিত হলেও এখনকার অনেক শাসক (মহাজন) অবহেলা করে থাকেন। বেতন ও অধিকারের ব্যাপারে অবহেলা করে। তাই এসব কবিতা এখনও প্রাসঙ্গিক। বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার চলমান সংগ্রামে নজরুলের কবিতা টনিকের মতো কাজ করতে সক্ষম। শতবাধা আসুক তবুও এগিয়ে যেতে হবে, শৃঙ্খলের বাঁধা ছিঁড়ে ফেলার উপলব্ধিই একমাত্র পাথেয়। এ উপলব্ধি আসলে আমাদের মধ্যেও জারিত হওয়া প্রয়োজন। আমরা বলি যথা বাধা-বিপত্তিই আসুক ছুঁড়ে ফেলি তা, প্রতিরোধ গড়ি; নজরুলের মতো বলি, ‘যতবার বাঁধি ছেঁড়ে সে শিকল,/মেরে মেরে তা’রে করিনু বিকল’।
নজরুল নিপীড়িত ও বঞ্চিত শ্রেণীর মানুষের কবি। শ্রেণীবৈষম্যের শিকার মানুষগুলোই হয়ে ওঠে তার কবিতার বিষয়বস্তু। জীবিকার জন্য শ্রমজীবী মানুষ নজরুলের কবিতায় স্থান পেয়েছে। তিনি তাঁর কবিতায় গণমানুষের ভাষা বা শব্দ ব্যবহার করেছেন। তিনি ছিলেন একজন গণমুখী সাহিত্যিক; ধর্মান্ধতা, অন্যায়-অবিচার, চরমপন্থা, শোষণ-তোষণ, নিপীড়ন ও সকল প্রকার বৈষম্যের বিরুদ্ধে সর্বদা প্রতিবাদী। নজরুলের ‘আমি’-এর মধ্যে খুঁজে পাই এক অদম্য মানবিক-চেতনা। বাংলা কবিতায় সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সবচেয়ে উচ্চকণ্ঠ কাজী নজরুল ইসলাম। কুলি-মজুর ও শ্রমিক শ্রেণির প্রতি দেখালেন গভীর সহমর্মিতা ও অকৃত্রিম ভালোবাসায় দরদ। শোষণ-মুক্তির আহ্বান জানান ক্ষণে ক্ষণে। সাম্যবাদী কাব্যের বীরাঙ্গনা,কুলি-মজুর, মানুষ, রাজা-প্রজা, নারী, পাপ, চোর-ডাকাত প্রভৃতি কবিতায় সাম্যবাদী নীতি প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। বাংলাসাহিত্যে তিনিই প্রথম সাম্যের গান গেয়েছেন, নির্যাতিত মানুষের সাফাই গেয়েছেন। মূলনীতি হিসাবে প্রচার করেছেন, ‘গাহি সাম্যের গান—/মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান’ (মানুষ)।
নজরুল দুর্নীতির বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেছেন যা প্রায় প্রতিটি সমাজে রয়েছে। এসব অপশক্তি স্বাভাবিক ও মানবিক সম্পর্ককে নড়বড়ে করে দেয়; উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করে। নজরুল অত্যাচারীদের মুখোশ খুলে দেন এবং শোষকদের বিরুদ্ধে দাঁড়ান। যারা সামাজিক শ্রেণি, মানব সম্পর্ক এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একটি সুস্পষ্ট ব্যবধান তৈরি করে থাকে এবং যেখানে মানুষ শান্তি ও সম্প্রীতি নষ্ট হয় সেসব অন্ধকারের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করেন।